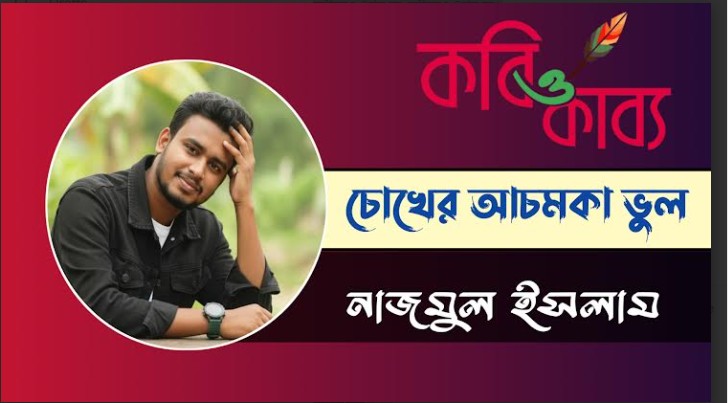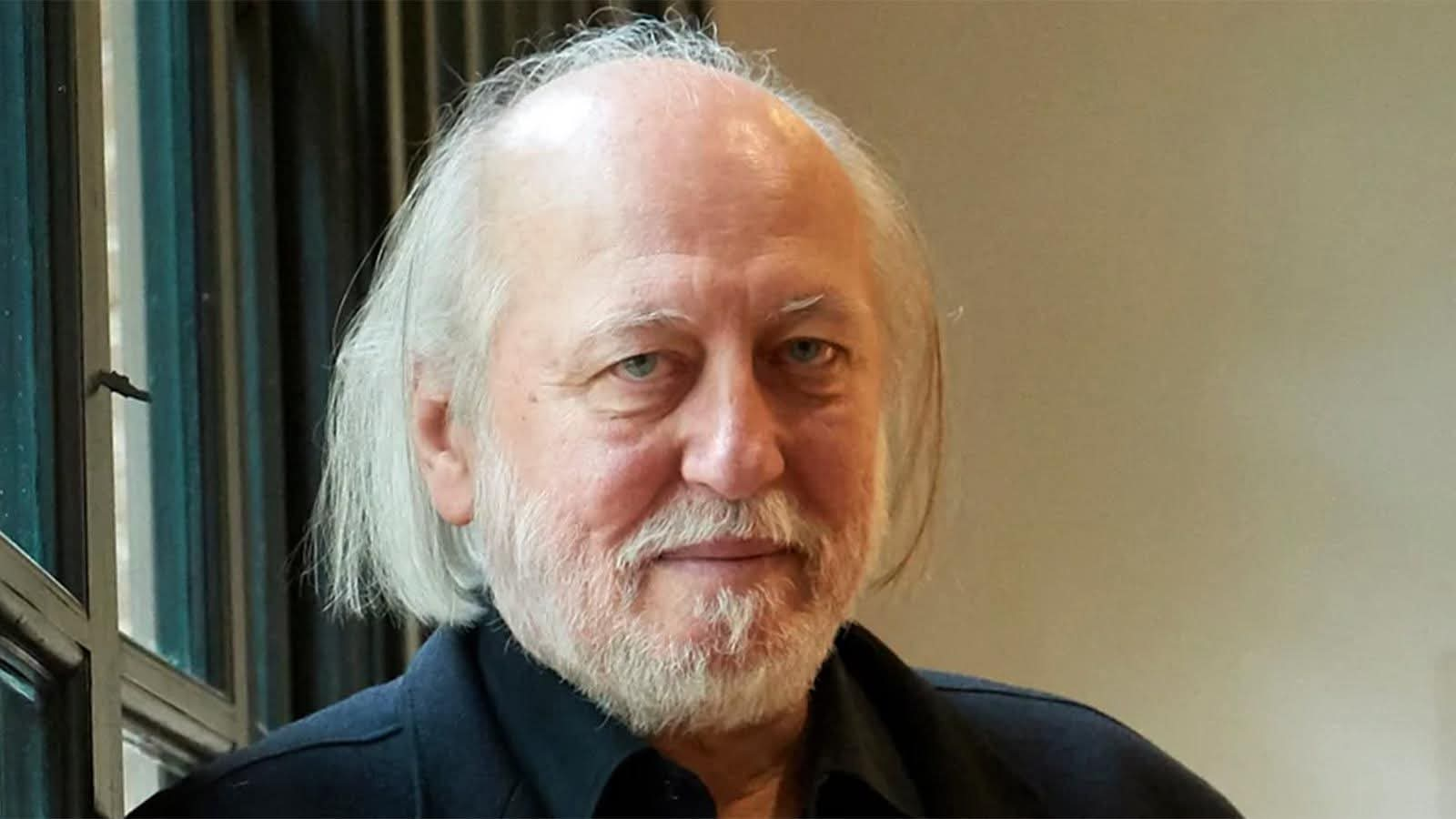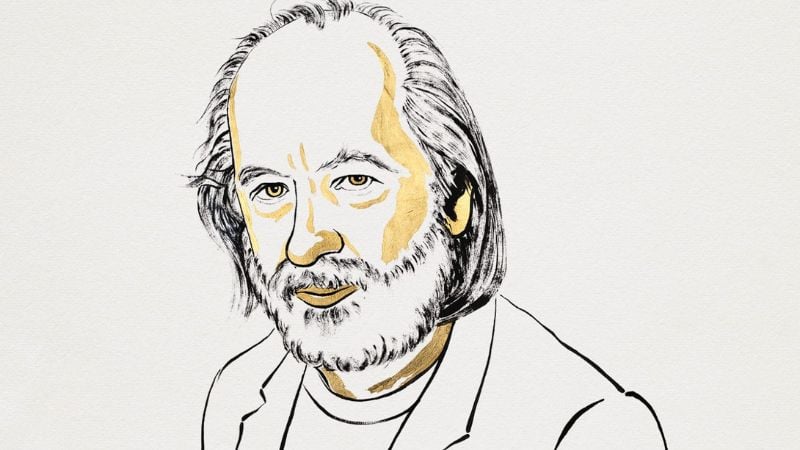Abstract
According to historical researchers, today's greater Noakhali township was built on the banks of the Meghnad by a mixture of sea mud and silt. About three and a half thousand years ago, during the Vedic period, the soil of this region became suitable for human habitation. Then the descendants of Kiratjati came down to the lowlands and settled at the foothills of Raghunandan Hills, bordering South Tripura i.e. Feni. [Source: Mr. Oranil, English surveyor, census report 1891 AD.] History researcher. According to Buchanal, in the evolution of time, in Yogidia village of today's Kompanyganj upazila, Pala Rajas' Sahiyogi Yugi Sanatani people are the original inhabitants of the region. Basically, they are the ones who introduced Pitha-Paesh-Puli Prasad after the first fall as a way to appease the god Bhogtushti. It is a colorful history of Pitha culture of this area.
চাবিশব্দ : মেঘনাদ-মেঘনা নদীর অপর নাম। কিরাতগণ-সমতট অঞ্চলের প্রথম ভূমিপুত্র। যুগী-বৃহত্তর নোয়াখালীর আদি মানব। নৈবেদ্য-দেবতাকে নিবেদিত উপাচার। হরিহরআত্মা-দেবতা বিঞ্চু ও শিবের একটি মিশ্ররূপ। মলঙ্গি-পাগি : পাগড়িধারী শ্রমজীবী মানুষ।
প্রেক্ষাপট : ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক
সারাৎসার: ঐতিহাসিক গবেষকদের মতে, আজকের বৃহত্তর নোয়াখালী জনপদ মেঘনাদের তীরে সমুদ্রের কাদা ও পলির মিশ্রণে পত্তন হয়েছিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেবৈদিক যুগে এ অঞ্চলের মাটি মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে। তারপর কিরাত জাতির বংশধরেরা নিম্নভূমিতে নেমে এসে দক্ষিণ ত্রিপুরা অর্থাৎ ফেনীর সীমান্তবর্তী রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে বসতি স্থাপন করে [সূত্র: মি. ওড়ানিল, ইংরেজ সার্ভেয়ার, আদম শুমারি রির্পোট ১৮৯১ খ্রি.]।
ইতিহাস গবেষক বুকানলেরমতে, কালের বিবর্তনে আজকের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার যোগীদিয়া গ্রামে পাল রাজাদের সাথে আসা সনাতনী লোকেরাই এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। মূলত তারাই ভোগতুষ্টি দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার উপায় হিসেবে পিঠা-পায়েস-পুলি প্রসাদের প্রবর্তন করেছিল। এটিই এই এলাকার পিঠা সংস্কৃতির এক বর্ণিল ইতিহাস উপাখ্যান।
বৃহত্তর নোয়াখালীতে মানব সমাজের যাত্রা ও পিঠা ঐতিহ্য : ইতিহাস গবেষকদের মতে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে মেঘনাদের তীরে সমুদ্রের কর্দম আর পলিমাটি মিশ্রিত একবিংশ শতকের গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাহু ঘিরে নোয়াখালীর ভূভাগ উত্থিত ও গঠিত। সে সর্ম্পকে স্পষ্টত ধারণা পাওয়া যায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজ গবেষক জে. ই. ওয়েবস্টার সম্পাদিত নোয়াখালী ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে। তাতে নোয়াখালী জেলা সর্ম্পকে বলা হয়েছে,
Youngest of all the districts of the Ganges ‘Delta”...This district most probably became fit for human habitation during the priod of the Vedas [1400-1000 B.C].1
প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে বৈদিক যুগে [খ্রিস্টপূর্ব পনেরশো অব্দ] এ অঞ্চলের মাটি মানব বসতির উপযুক্ত হয়। তখনকার কিরাত জাতির কিরাতগণ উঁচু ভূমি থেকে নীচু ভূমিতে নেমে আসে এবং কিরাত আলয় অর্থাৎ বর্তমান সিলেটের দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর পূর্বাংশে পার্বত্য অঞ্চল ঘিরে বসবাস শুরু করে। জাতি উৎস্য ক্রম বিকাশে এরা সম্ভবত মঙ্গোলীয় জাতীয় চন্ডাল শ্রেণি অথবা ভোটচীনা গোষ্ঠির লোক। প্রথম এ অঞ্চলের কিরাত নামক স্থান বর্তমান দক্ষিণ ত্রিপুরা তথা ফেনীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রঘুনন্দন পাহাড়ের পাদদেশে কিরাতগণ মানব বসতি শুরু করে। [তথ্যসূত্র : মি. ওডানিল, ইংরেজ সার্ভেয়ার, আদমসুমারি প্রতিবেদন ১৮৯১ খ্রি.]
ইতিহাস গবেষক ড.বুকানলের মতে, কালবিবর্তনে আজকের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় যোগিদিয়া গ্রামে পাল রাজাদের সাথে আসা যুগী উপাধিধারী সনাতনী লোকেরা এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী।২
এ জেলায় যোগসাধনার পাশাপাশি প্রথম তাঁরা বস্ত্রবয়ন ও লবণ শিল্প উৎপাদন এবং একটি চিরায়ত আদর্শিক জীবন যাপন শুরু করেন। বস্ত্রবয়ন তাঁতিদের সম্বোধন করা হতো যুগী অন্যদিকে লবণ উৎপাদনকারীদের অভিহিত করা হতো মলঙ্গী ও পাগী। স্থানীয় সংস্কৃতিতে যুগীরা ধর্মীয় উপাসনার পাশাপাশি যোগ করেন নানান আচার-উপাচার জীবনানুসঙ্গ। ধারণা করা হয়, দেবতার ভোগতুষ্টি, নৈবেদ্য উপাচার হিসেবে তাঁরা প্রথমে ফলান্ন, পরে পায়েশ, প্রসাদ ভোজনরীতি চালু করেন।
সেই সময় কৃষি প্রধান সমাজে ধান ছিল প্রধান খাদ্যশষ্য। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবে চালের গুড়ো দিয়ে তৈরি পিঠা-মিষ্টান্ন কৃষিজীবি বাংলার মানুষের কাছে তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং কখনও কখনও তা ধর্মীয় আরাধনার উপযোগেও যুক্ত হয়। যা কালান্তরে অপরাপর স্থানীয় জাতি গোষ্ঠির দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক আহাররীতিতে এবং সামগ্রিক বাঙালি সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীকে পরিণত হয়। তাই আজ আমরা জানবো প্রাচীনকালে কৃষি প্রধান সমাজে নোয়াখালী পিঠা সংস্কৃতির সেই বর্ণিল উপাখ্যান, যেখানে সমুদ্রের ভূমি এবং সমুদ্র সন্তানেরা ধারণ করে আছে সুরচঞ্চল লোকায়তজীবনের অনিঃশেষ উপাদান-উপকরণ।
আদি উৎসরণ ও অবয়ব : সংস্কৃত শব্দ ‘পিষ্টক’ থেকে বাংলায় পিঠা শব্দের উদ্ভব। যার অর্থ : বাটা বা পেষা হয়েছে এমন। বহুধা অর্থ : চূর্ণিত, দলিত, মিশ্র রসায়ন। মূল উপকরণ চালবাটা, ময়দা, আটা, নারকেল, অন্যকোনও শষ্যজাত গুড়ো, গুড় কিংবা চিনি সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ। কার্যত বহুমাত্রিক উপকরণ মিশ্রিত হয়ে সময়ের চাহিদা বিবেচনায় পারিবারিক ও সামাজিক রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠানে অর্নিবার্য নানন্দিক অনুসঙ্গে পরিণত এবং পরিবেশিত হয়। এটি একদিকে মুখরোচক মিষ্টান্ন/ঝাল খাবার অন্যদিকে ঐতিহ্যের ধারক বাহক এবং সমাজ জীবনের নিখাদ সংস্কৃতি মুন্সিয়ানা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, অসম অঞ্চলে পিঠার ঘরোয়া-রীতি প্রচলন দেখা যায়। বাঙালির খাদ্য তালিকায় পিঠপিুলির তালিকা বেশ দীর্ঘ। যাতে রয়েছে অন্তর আবেগ, মননশীলতা আর সৌজন্যতা।
ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে নোয়াখালীর পিঠা : প্রাচীন বাংলায় পিঠার ইতিহাসের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের অনিন্দ্যসুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন : পৌষ সংক্রান্তি, বৈশাখি, শারদীয় দুর্গা, লক্ষ্মী পূজা ইত্যাদি উৎসবে পিঠা তৈরি ও খাওয়ার বহুল প্রচলন রয়েছে তেমনি বিয়ের অনুষ্ঠানেও। জামাই আদর আর আত্মীয়তা স্থাপনে পিঠা সেতুবন্ধনের ভূমিকা রেখেছে নিরন্তর। পিঠা ভোজনরসিক এখানকার মানুষেরা একে এমন এক ধ্রুপদ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে বাংলার কবি গবেষকদের কলমে বারবার তা আলঙ্করিক দৃষ্টান্তরূপে উঠে এসেছে।
পিঠার বিকাশ ও রূপান্তর : ‘যুগ-যুগান্তরে পিঠার কাঠামো অঙ্গসৌষ্ঠব, স্বাদ, রুপ-মাধুরী, বৈচিত্র্যতা, পরিবেশন দক্ষতা, সৌন্দর্যরীতি, রুচি, উত্তরোত্তর নতুন অবয়বসৃষ্টি পিঠা অনুরাগিদের চিন্তা দর্শনে ব্যাপক ছাপ ফেলে। বিশেষত স্থানীয় রমণীরা রূপ-রুপান্তরের ভেতর দিয়ে নানান পিঠার ঐতিহ্য সুনাম ও কদর বাড়াতে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন তাঁদের প্রেম ও শিল্পীত হাতের ছোঁয়ায়। পিঠা আন্দোলন চর্চায় মিলেমিশে এক হয়ে যায় আপামর বাঙালি রমণী, হৃদয় বলে ওঠে কবিগুরুর ভাষায়, “ওলো সই, ওলো সই..আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই। ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোণে বসে কানাকানি, কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই “
মধ্যযুগে পিঠা তৈরি ও প্রচলন বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন উৎসব ঘিরে পিঠার আবহ সৃষ্টি হয়। পিঠা তৈরি, খাওয়া এবং ঘরে ঘরে পারস্পরিক সৌহার্দ বিনিময় প্রথা তখন থেকেই শুরু হয়। এই সময় থেকেই বাংলার অধিকাংশ পিঠার আকৃতি রূপান্তর ও বিচিত্র্যভাব আসে—যা রসনা বিলাসে জৌলুস বাড়ায়, কখনওবা তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। আধুনিক যুগে বাংলা পিঠার আরও বিকাশ বিস্তৃতি ঘটেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, ভৈরব, খুলনায়।
স্থানীয় পিঠার প্রস্তুত প্রক্রিয়া : বাংলার নিজস্ব আদিম অভিজাতপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য হিসেবে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পিঠে সাধারণত মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকলেও ঝাল, টক বা অন্য যে কোনও স্বাদের হতে পারে। পিঠের প্রস্তুত প্রণালী দু’ধরনের হয়ে থাকে। যেমন : ১. রন্ধন প্রক্রিয়া ২. শুষ্ক মাধ্যম প্রক্রিয়া।
পিঠার প্রস্তুতকরণ শ্রেণি তিন প্রকার : ১. তেলে ভাজা ২. তেল বিহীন ৩. সিরাযুক্ত।
ঢেঁকি ও পিঠার যুগলবন্ধী সর্ম্পক : বাঙালি জীবনে ঢেঁকি ও পিঠার যুগলবন্ধী সর্ম্পক আজও অমলিন। বাঙালির পিঠা সংস্কৃতির ইতিহাসে ঢেঁকিচাঁটা চালের গুড়ি পিঠা তৈরির অনস্বীকার্য উপকরণ। প্রযুক্তি প্রসারে ঢেঁকির ব্যবহার কমে এলেও বিশেষত গ্রাম বাংলার রসুইঘরে ঢেঁকির ব্যবহার এখনও কাল সাক্ষী হয়ে আছে।
প্রাত্যহিক জীবনে পিঠার কদর : জেলার গ্রাম কিংবা নগরে নাগরিক জীবনে পিঠা খাওয়ার সুযোগ রয়েছে। গ্রাম জীবনে পিঠা তৈরি সহজাত হলেও শহুরে ব্যস্ত জীবনে পিঠা তৈরি করা কষ্টসাধ্য বিষয়। তবে আশার কথা অনেক ঋদ্ধপ্রাণ মানুষ রসনা তৃপ্তি মেটাতে পিঠা রন্ধন উপকরণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ ও পিঠা তৈরি করে থাকেন। পরিবারের সদস্যবর্গ তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ঘরদোর মাতিয়ে তোলেন। সারা বছর পিঠার সর্বজনীন ব্যবহারকে প্রধানত তিনটি পর্বে সাজানো যায়। যেমন : বারোমাসি, ঋতুভিত্তিক, উৎসব/অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক। তবে সচরাচর গায়ে-হলুদ, জন্মদিন আকিকা, বিয়ে সমন্ধ স্থাপনে, বিয়ে বাড়ির ফিরানিতে ও বৌ-ভাতে পিঠা আদৃত এবং সমাদৃত হয়ে থাকে।
পিঠাপুলি ও পায়েশ, ফিরনি ব্যঞ্জন : এইসব দিনরাত্রির চক্রে বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষের ঘরোয়া ও বাহির বাড়ির সামাজিক অনুষ্ঠানে পিঠা সংস্কৃতির অপরিহার্য ব্যঞ্জন হিসেবে চাল চিনি দুধ মিশ্রণে ক্ষীর বা পায়েশ, ফিরনি, জর্দাভাত ব্যঞ্জন তৈরি করা হয়। এগুলোতে পেস্তা, বাদাম, কিসমিস মিশিয়ে আরও উপাদেয় এবং শৈল্পিক সৌজন্যতায় পরিবেশন করা হয়। সনাতনী হিন্দু পরিবারে ক্ষীরের নাড়ুর প্রচলনও রয়েছে। ছাঁচে ফেলে নকশি নাড়ু তৈরি করা হয়। যেমন : স্বস্তিকা, ফুল, ফল, পুতুল, মাছ ইত্যাদি প্রকৃতির নাড়ু। এ নাড়ু আবার দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবদ্যও দেওয়া হয়।
পিঠা তৈরিতে মেয়েলি কথার ফুলঝুরি : আমাদের গাঁও-গেরামে বিশেষত বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে পিঠা পায়েশ তৈরির সময় রমণীরা পান খেয়ে লাল ফিকে মুখ রাঙিয়ে তোলেন আর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একান্তে খোশ গল্পে মেতে ওঠেন। যেখানে জীবনের অকথিত কথা উছলি পড়ে। বয়সের ব্যবদান ঘুচে যায় নবীন-প্রবীণ আর যুবার রসালাপে, কানাকানিতে সর্ম্পকের দূরুত্ব কমিয়ে পিঠা তৈরির ক্ষণটিকে প্রত্যেকে মধুময় করে তোলেন। এ যেন এক জীবনে অজস্র জীবনের মধুরিমা। সবাই হয়ে উঠেন একে অপরের হরিহর আত্মা।
কথায় কথায় জনৈক প্রবীণা এক কিশোরীর উদ্দেশ্যে ফুলঝুরি ছুঁড়ে দেন এভাবে—এ্যা ঢেমনীর দেমাক কত? দেখছোনি হিতির গাততুন লাগে যে ত্যাল টেবাই টেবাইনা হড়ের!
লোকগান-ছড়ায় পিঠার আবাহন : ঊনিশ শতকে পিঠা তৈরির সন্ধিক্ষণে নারী-পুরুষের কন্ঠে আরব্য রজনীর প্রেম-প্রণয়োপাখ্যান সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল যাত্রাপালার গান গীত হতো। বলা যায় এ গান সবার মুখে মুখে ফিরত।
এখানে তার দুটো চরণ উদ্ধৃত হলো। “আয়লো ভগ্নি জামালপরী আয়লো একবার ছুটে আয়, মালকাবানু দেখবি যদি আয়লো একবার ছুটে আয়”।অন্যদিকে পৌষ পার্বণে শীতের সাইন্না পিঠা নিয়েও লোকজীবনে রয়েছে মজার ছড়া। যেমন : “ছাইন্না হিড়া শীত কালে/মা বানাই দিছে, দুলা ভাইরা আংগো বাড়ি/আপুরে লই আইছে। গেরাম-গঞ্জে ছাইন্না হিড়া/বাড়ি বাড়ি যায়, তালতো বইন হিঁড়াত বই/মজা করি খায়।
নোয়াখালীর পিঠায় খেজুর রস ও ঋতুর প্রভাব : সমগ্র পৌষ-পার্বণ পিঠা-পায়েসের চিরায়ত উৎসব। ঘরে বাইরে চলে ধুমধাম পিঠাপুলির মহোৎসব। নোয়াখালীর প্রায় সর্বত্র খেজুর গাছের আবাদ লক্ষ্য করা যায় তবে অধিক হারে চরাঞ্চলে খেজুর গাছ আবাদ এবং রস আহরণ দৃশ্যত চোখে পড়ে। শীত মওসুমে গাছিরা বিরূপ শীতল আদ্র আবহাওয়ায় খেজুর গাছ কাটেন ও গাছে চোঙ লাগিয়ে হাঁড়ি কলস চাপেন এবং কাক ডাকা ভোরে রস সংগ্রহ করে আনেন।
খেজুরের রস কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাতকৃত নানাবিধ গুড়, আখাই মিঠাই পিঠা-পায়েস, শিরনি তৈরি, স্বাদে অকৃত্রিম দ্যোতনা সৃষ্টি করে। রসনা সিক্ত হয় টইটম্বুর রসে, মন রাঙ্গে সে রস আস্বাদনে। জাগে প্রভাত অনাবিল হাসি আনন্দে আর জীবনপুরের হেঁসেলে পরম মমতায় বাংলার মায়েরা সে পিঠেপুলি শিল্পের পূর্ণতা দেন। তখন বউ কথা কও গেয়ে উঠে গান। পূর্বাচলে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দেয় রবি। গগণ মাদুর হেসে খলখল।
পৌষ-পার্বণে স্বাতন্ত্র পিঠাপুলি-পায়েশ : এতদাঞ্চলে ঋতুভিত্তিক পিঠা-পায়েশের মধ্যে শীতকালেই বহুমাত্রিক পিঠা সংস্কৃতির অনন্য ব্যঞ্জন প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। শীতকালীন প্রধান পিঠাগুলো হচ্ছে—সানকি পিঠা, চিতই/চিতল পিঠা, ছাইন্না পিঠা ভাপা পিঠা, খোলাজালি/খোলাজাঁক পিঠা, পাটিসাফটা পিঠা, মুঠকি পিঠা, লৎ পিঠা, ছুটকি পিঠা, ম্যারা/ম্যাড়া পিঠা ইত্যাদি।
পিঠার প্রকারভেদ : প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে প্রধানত তিন শ্রেণির পিঠা পায়েশ পুলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ১. দেশিয় সংস্করণ ২. বিদেশি সংস্করণ ৩. দেশিয় সংস্করণের রূপান্তরিতধারা।
১. দেশিয় সংস্করণ পিঠাগুলো হলো : পানতুয়া, খোলাজা/খোলাজালি, ছাইন্না, পাক্কন, পাটিসাফটা, নারকেলপুলি, দুধপুলি, লৎ, চিনিজালি, কলাপাতা, চিতই/চিতল, ভাপা, মুঠকি, সুজিপিঠা, সুজির রসভরি, দুধছিটা রুটি, হানকি/সানকি, জিলাপি, ভাজাপুলি, দুধভক্তি, সিঙ্গারা, কুলশি, রসপান, কিমা, তালেরবরা, ফুলঝুরি, খেজুরগুড়, মোয়া/নাড়ু, রস পাবান, কাটা পাকান, ফুলপুলি, সবজিপিঠা, তালের পিঠা, লুচি, ছুটকি, ঝিলমিল, গুলগুলা, দুধসন্দেশ, রসকদম, ক্ষীরের পাক্কন, রস ছয়কলি, ঝাল পাটিসাফটা, ঝালপুলি, মহুয়া, ফলপিঠা, দুধ গোলাপ, দুধ খেজুর, ক্ষীরসা পাটিসাফটা, এলাচি লবঙ্গ, আলুপিঠা, ঝুনঝুনি, পুলি পাবান, শাচ, লস্কর, পাস, ধুইপিঠা, সেমাই এবং শসার মোরব্বা পিঠাসহ প্রায় ৬০ সংখ্যাধিক পিঠার সমাহার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।
২. বিদেশি সংস্করণ : ডিম মল্লিকা, চিকেনচাপরুটি, ফাল্গুনি, কদম চিকেন, মুগ পাক্কন, ছুই/শেওয়া, নারকেল পাতা, ফ্রুটি প্যানকেক, চিকেন নুড়লস রোল, সবজি ঝালপুলি, চিকেন নিমকি, মালাইচপ, সুজির সন্দেশ, ডিমচকো পানতুয়া, চিকেন চিংড়ি, ঝালপুলি, তরী, ডিমসবজি রুই, সবজি রোল, চেরি রস খেজুর পিঠা, ফুলঝুরি, ডিমসুজি পাক্কন, ফুল মাধুরী, চিকেন মনপুরা, ডিমের কলসি, চিকেন অনথন, কিমাপুরি, ঝালরুই, গাজর সন্দেশ, চিকেন মমসহ প্রায় পঁয়ত্রিশ অধিক পিঠাপুলি।
৩. দেশিয় সংস্করণের রূপান্তরিতধারা : হানকি>বিবিখানা, শাচেরপিঠা>ফুলঝুড়ি, পানতুয়া>ডিমসুন্দরী, লস্কর>গোপুল, নারকেল পাবান>শর্পিরুটি, পাস>পুলি, ধুইপিঠা>ভাপাপিঠা, সাইন্না> ম্যাড়া পিঠা ইত্যাদি।
পিঠা বিপনন : ১. স্থায়ী কাঠামো বাণিজ্য ২.অস্থায়ী/ভ্রাম্যমাণ সড়ক বাণিজ্য।
১. স্থায়ী কাঠামো বাণিজ্য প্রদর্শনী : বিগত একদশকে স্থানীয়ভাবে পিঠাপুলি পায়েশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বাণিজ্য প্রসার ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে জেলারসদর ও রাজধানী ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে। স্থানীয় পিঠা শিল্পকে ঘিরে কর্মসংস্থান, রসনাবিলাস, রূচিবৈচিত্র্যতা, পিঠা প্রদর্শনীর মতো অভিজাত পরিবেশ সর্বপরি চিত্ত বিনোদন-অবসর অবকাশ গড়ে ওঠেছে।
২. অস্থায়ী/ভ্রাম্যমাণ সড়ক বাণিজ্য প্রদর্শনী : পিঠাপুলির স্থায়ী কাঠামো বাণিজ্যের বাহিরে উৎসব/অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক বাণিজ্য বিপণন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলারসদরের প্রধান সড়ক, অলিগলি, উপজেলাসদর ও হাটবাজারে বেশকিছু ভ্রাম্যমান ট্রলি গাড়িতে পিঠাপুলি বিক্রয় হতে দেখা যায়। স্বল্প মূল্যে এসব পিঠপিুলি খদ্দেরদের রসনাতৃপ্তি যুগিয়ে থাকে।
প্রতিফলন : বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষের চিরায়ত অকৃত্রিম মানব দরদ, আন্তরিকতা প্রকাশ পায় তাদের সার্বজনীন আতিথেয়তায়। আচার-রীতিতে ফুটে উঠে তাঁদের স্বভাবসুলভ নির্মলহাসি। সামাজিক বন্ধন আর কৃষ্টি সংস্কৃতিতে পিঠা পায়েশ পুলি নিয়ত সৃজনশীলতার উদাহরণ রাখছে—নিঃসন্দেহে এটি আমাদের ঐতিহ্যের স্মারক বহন করছে। তাই হয়তো মধ্যযুগের কবি ভারত রায় গুনাকর তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলেছিলেন, “আমার সন্তান থাকে যেন দুধে-ভাতে”।
উপসংহতি : একটি শিল্প ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই নিরন্তর উদ্যম, শক্তি, ভালোবাসা আর সবার সহযোগিতা। আমরা সেই সুদিনের প্রত্যাশি। এখন আত্মোপলদ্ধির সময়, অতীত ফাল্গুনে আমরা সংগ্রাম করেছি।তাই অমর কথাশিল্পী জহির রায়হান বলেছিলেন, “আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুন হবো”।
তথ্য ঋণ :-
১.এ.কে.এম মক্রমবিল্যা ও শ্রী অশ্বিনী কুমার সোম তত্বনিধি এবং শাবিহ মাহমুদ সম্পাদিত নতুন সংস্করণ ২০২২খ্রি.: নোয়াখালীর ইতিহাস ১৯৩০ খ্রি. রেড়িয়েন্ট প্রেস, কাঁটাবন, ঢাকা,।
২.শ্রী প্যারীমোহন সেন : নোয়াখালীর ইতিহাস ১৮৭৬ খ্রি.পৃ. ২৫-২৬,বইপত্র ৩৮/৪, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, জুলাই ২০০৭ খ্রি.।
৩.কাজী মোজাম্মেল হক :তিন হাজার বছরের নোয়াখালী ১৯৮২ খ্রি., পৃ. ১২-১৩, মূলসূত্র : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৯১৮ খ্রি. ২য় সংখ্যা পৃ. ৬৩-৬৮, কলকাতা, প.বঙ্গ, ভারত।
৪.শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ : রাজমালা ১৩০৩ বঙ্গাব্দ,পৃ : ২৯-৩০, গতিধারা ৩৮/২ক, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.।
৫.আবদুল গণী : প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক ভূগোল ১৯০০, পৃ.৪৮, ১৩৫ -, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৬.জে. ই. ওয়েবস্টার সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার ১৯১১ খ্রি. নোয়াখালী।
৭.জমির আহমেদ :ফেনীর ইতিহাস ১৯৯০, পৃ. ২৩ -, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।
৮.কমল চৌধুরী :নোয়াখালী ও সন্ধীপের ইতিহাস ২০০৯, পৃ. ৩৫-৩৬, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প.বঙ্গ, ভারত।
৯.জহির রায়হান :আরেক ফাল্গুন, পৃ : ৭২, অনুপম প্রকাশনী ১৯৯৮ খ্রি., ৩৮/৪, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০,ঢাকা, বাংলাদেশ।
১০.ড.ওয়াকিল আহমদ :লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা ২০০৭, ৭ম খন্ড, পৃ. : ২২৭-২২৯ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
অনলাইন সহায়ক মাধ্যম :-
1. http://www. bangla.bdnews24.com/
2.http://www.somewhereinblog.net
3.http://www.deshiranna.com/
4.http:// www.arthosuchak.com/
5.http://www.beshto.com/
6.http://www.facebook.com/rakamarirannashikhun/
7.http://www.noakhalipithaghar.com/
8.http://www.priyo.com/
9.http://www.manobkantho.com/
10.http://www.bn.wikipedia.org/ Ges Lvevi `vevi †iwmwc
11.http://www.regalbangla.blogspot.com/
12.http://www.bangaliebook.com/
লেখক : কবি ও লোকগবেষক,নোয়াখালী।