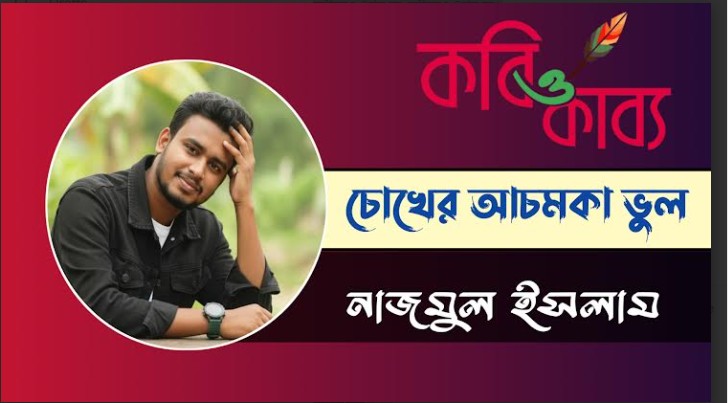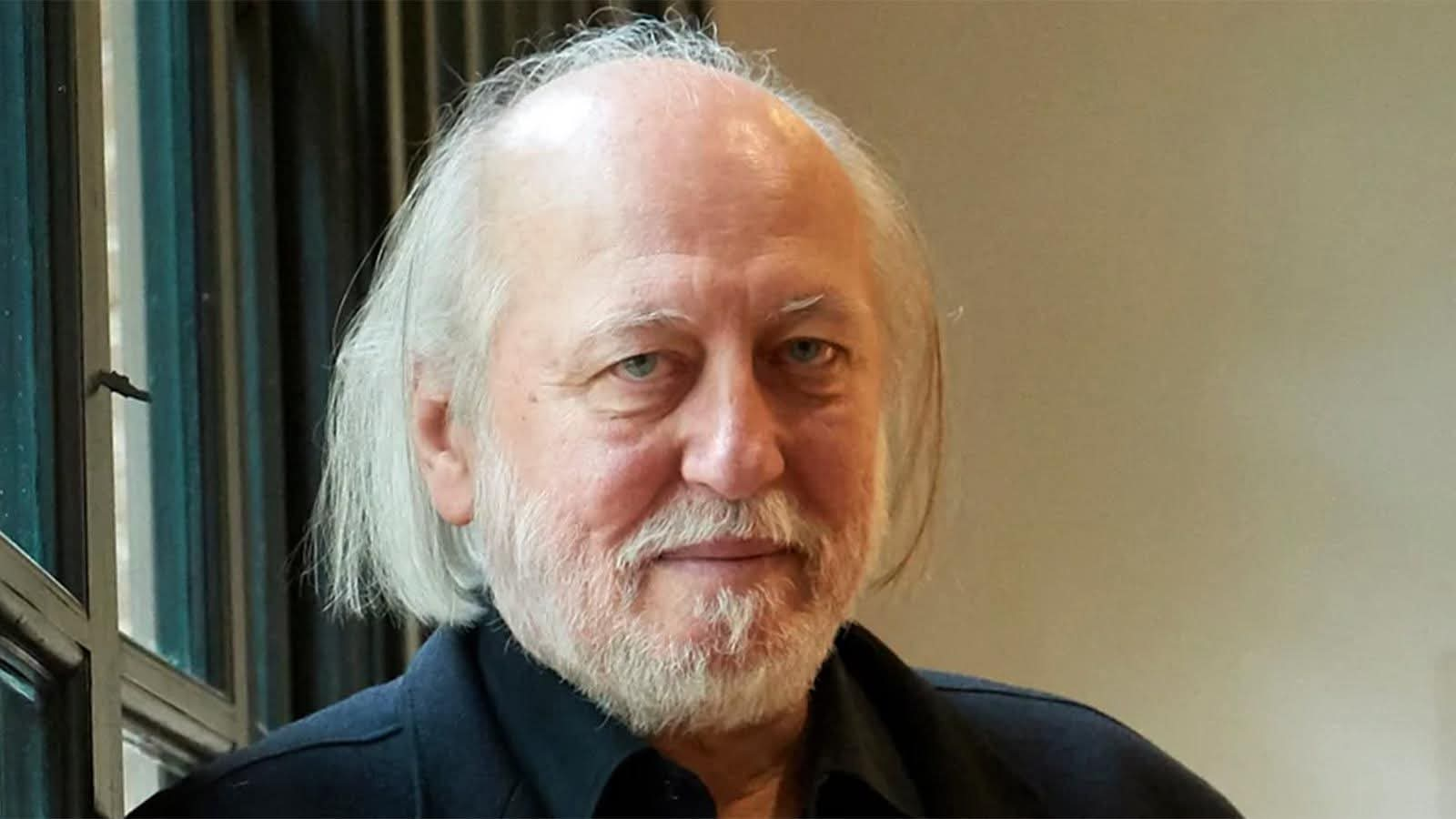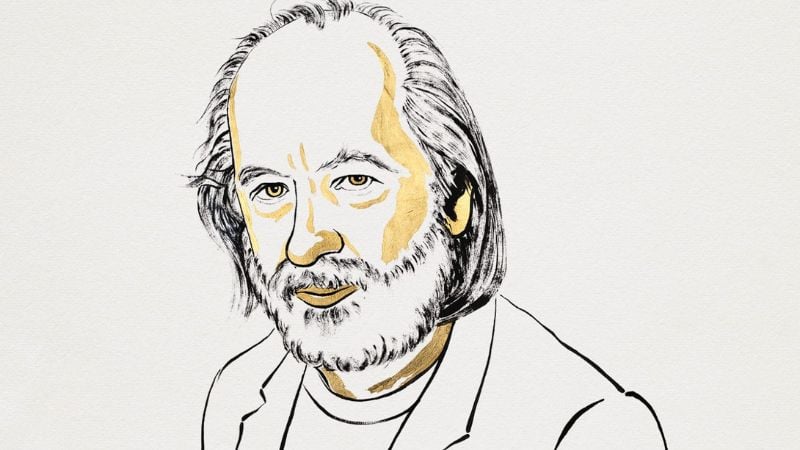এক.
মনসা দেবীর লোকভিত্তিক জন্ম কাহিনী বা মিথটি বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোককথা অনুযায়ী, মনসা ছিলেন মহর্ষি কশ্যপের কন্যা এবং এক মতে শিবের মানস কন্যা। দেবতারা তাঁকে স্বীকৃতি দিতে চাননি বলে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য সাপকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। মনসা দেবী সাপে কামড়ানো মানুষের প্রাণ রক্ষা করেন, সুতরাং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখা মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী এই বিশ্বাসকে আরও গভীর করে তোলে, যেখানে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা না করায় তাঁর ছেলে লখিন্দরের মৃত্যু ঘটে এবং বেহুলা মনসাকে তুষ্ট করে তাঁর স্বামী লখাই বা লখিন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এই কাহিনী রাজবংশী সমাজেও বিস্তৃতভাবে প্রচলিত এবং এর মাধ্যমে মনসা পূজার প্রথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে এসেছে।
সার্বিকভাবে, রাজবংশী সমাজে মনসা পূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি প্রাকৃতিক বিপদের প্রতিরোধ, সামাজিক একতা এবং লোকবিশ্বাসের এক মহৎ প্রতিফলন। কেলেকড়া ভক্ষণ, পূজার নির্ধারিত মাস, ও মনসার লোকমিথ–সব মিলিয়ে এটি একটি সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্যের নিদর্শন।
দুই.
রাজবংশী সমাজব্যবস্থায় মনসা পূজা একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয়। এই পূজা সাধারণত বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে, কারণ এই সময়ে সাপের উপদ্রব বেশি থাকে এবং মনসা দেবীকে সাপের দেবী হিসেবে পূজা দেওয়া হয় যাতে সাপের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাজবংশী জনগোষ্ঠী, যারা মূলত উত্তরবঙ্গ ও কুচবিহার অঞ্চলে বসবাস করেন, তাদের সমাজে মনসা পূজার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি শুধুমাত্র ধর্মীয় আচরণ নয়, বরং সামাজিক বন্ধনের মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত।
এই পূজায় নিরামিষ আহার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং এই সময় কলাগাছের কচি অংশ অর্থাৎ কেলেকড়া দিয়ে রান্না করা পদ গ্রহণ করা হয়। কেলেকড়া ভক্ষণ ও মনসা পূজার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। কলাগাছ হিন্দু সংস্কৃতিতে একটি পবিত্র গাছ হিসেবে বিবেচিত, এবং অনেক পূজায় এর ব্যবহার দেখা যায়। পূজার দিন ব্রত পালন করা হয়, যেখানে ভক্তরা পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস পরিহার করেন এবং সহজ, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন। এই নিরামিষ আহারে কেলেকড়া বা কাঁচকলা ব্যবহৃত হয়, যা লোকাচার অনুযায়ী শরীর ও আত্মাকে বিশুদ্ধ রাখে বলে বিশ্বাস করা হয়। অতএব, কেলেকড়া খাওয়া শুধু একটি খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং এটি পূজার ধর্মীয় শুচিতা ও সাংস্কৃতিক মান্যতার অংশ।
তিন.
মনসা পূজা উত্তরবঙ্গের কৃষিভিত্তিক সমাজ ও সংস্কৃতির ভেতর এক অপরিহার্য আত্মিক সংযোগের সুতোয় গাঁথা, যা শুধু একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং কৃষিজীবনের অনিবার্য অংশ, নারীর সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি। এই অঞ্চল, যেখানে মাটি, বৃষ্টি, ফসল ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ, সেখানে মনসা পূজা হয়ে ওঠে এক প্রতিরক্ষামূলক বিশ্বাস, যা সাপের ভয়ের চেয়ে গভীরতর—এক অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার প্রতিকার।
উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ চাষাবাদের ভূমি, বিশেষ করে বনজঙ্গল ঘেরা জনপদ ও নদীবিধৌত তীরবর্তী গ্রামগুলিতে মনসা পূজা মূলত সনাতন নারীদের দ্বারা লালিত ও সংরক্ষিত এক ব্রত। এই ব্রত শুধুই পারিবারিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিষেধক, সন্তানের রক্ষাকবচ, ফসলের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুস্থিতির প্রতি এক মৌন কিন্তু দৃঢ় আহ্বান। ফণা এখানে প্রতীক—অজানা আশঙ্কা, রোগ, দারিদ্র্য কিংবা অসময়ে প্রকৃতির প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে নির্ভরতার আশ্রয় স্থল। দুঃখের স্রোতে বহমান সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক অস্থিরতার মধ্যেই নারী তাঁর দৈনন্দিন ক্লান্তি ও সংকোচ ভেঙে, মনসার পাটে বসে নির্ভরতার দেবীকে আহ্বান জানান।
লোককবিতায়, গীতে, রাধার পাটে কিংবা বাস্তবে ঘরের কোণে বাঁশের কঞ্চি বেয়ে উঠে যাওয়া মনসার উপস্থিতি যেন উত্তরবঙ্গের নারীর এক অন্তর্গত শক্তির নিঃশব্দ উচ্চারণ। ব্রতের নিয়মে আছে উপবাস, কেলেকড়া ভক্ষণ, দুধ, কলা ও চাল দিয়ে পূজা—এসব পদ্ধতি যতটা ধর্মীয়, ততটাই সাংস্কৃতিক। নারী এখানে পুরোহিত নয়, অথচ তিনিই পূজার প্রধান পুরোহিতার ভূমিকায়, তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয় মনসার গান, তাঁর হাতেই তৈরি হয় দেবীর প্রতীক, তাঁর বিশ্বাসেই রচিত হয় দেবীর আসন। এই ভাবে উত্তরবঙ্গের কৃষিনির্ভর সমাজে নারী হয়ে ওঠেন আধ্যাত্মিক কুলাধারিণী, কেবল সংসাররক্ষিণী নন, বরং বৃহত্তর সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।
এই অঞ্চলে মনসা পূজার একান্ত নিজস্বতা হল এর সমবেত চরিত্র। পরিবার নয়, একটি পাড়া, একাধিক গৃহবধূ একত্রে পূজা করেন। এতে গড়ে ওঠে এক নির্জন ধর্মীয় গাম্ভীর্যের এক উজ্জ্বল সামাজিক বন্ধন। নারী একে অপরের পাশে বসে দিনভর কথপোকথনের রীতি আর ভক্তিভরা গলায় মনসার লোকপ্রশস্তির সুর তুলেন, মাটির প্রতিমা কিংবা চিত্রলিপিতে মনসার প্রতিচ্ছবি আঁকেন। এই চিত্রভাষা, এই কথোপকথনের শিল্প—উত্তরবঙ্গের নারী জীবনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যর এক নিজস্ব ধারা।
তবে সময় বদলেছে। এখন মনসা পূজার আচারগত বাহার অনেকক্ষেত্রেই কমে এসেছে, কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা একেবারে ফুরায়নি। আজও বন্যা, নদীভাঙন, কৃষিক্ষেত্রে অজানা পোকামাকড়ের হানা বা সন্তানের অজানা রোগে মানুষ মনসার আশ্রয় খোঁজে। অনেকে হয়তো আগের মতো আচারনিষ্ঠ নন, কিন্তু ব্রতের এই সমষ্টিগত উপলক্ষ এখনো নারীকে একযোগে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সংহত করে—যে সমাজ তাকে অবিরত শ্রমের ভারে চেপে রাখে, সেই সমাজেই সে মনসা ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে একদিন অন্তত নিজের মতো করে কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিছু চাইতে পারে, কিছু রক্ষা করতে পারে।যা কোচ-রাজবংশী সংস্কৃতির ভেতরে মনসাবন্দনার একটি মৌলিক শিল্পরূপে পরিণত হয়েছে।
স্থানভেদে হয়তো মনসার নাম পদ্মা, কোথাও বিষহরি—কিন্তু নারীসত্তার আত্মমর্যাদা, বিশ্বাস ও পরিবাররক্ষার ঐকান্তিকতা সর্বত্রই এক। এখানেই মনসা পূজার শাশ্বত চারিত্র উন্মোচিত। দেবী এখানে প্রতীক—যিনি নারীকে দিয়ে সমাজকে রক্ষা করান, নারীকে দিয়ে প্রকৃতিকে প্রশমিত রাখেন, নারীকে দিয়েই ভবিষ্যতের ভিত গড়েন।
মনসা পূজা তাই উত্তরবঙ্গের কৃষিপ্রধান জীবন ও নারী নেতৃত্বাধীন ব্রতসংস্কৃতির এক আন্তরিক জাগরণ—মাটি, নদী, সন্তান ও সংসারের সংকটপূর্ব মুহূর্তে এক নীরব কিন্তু গভীরভাবে সমাজ-প্রতিসংলগ্ন আচার, যা সময় বদলালেও তার হৃদয়াবেগ হারায় না। উত্তরবঙ্গের আকাশে যখন শ্রাবণের মেঘ জমে, তখন প্রতি নারী যেন বেহুলা, একা হাতে কলার ভেলা বেয়ে পাড়ে তোলেন মনসা-ভক্তির সেই দীর্ঘ স্রোত।
চার.
আষাঢ়ের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে, যখন বর্ষার নীলচে অন্ধকার মেঘে আকাশ ঢেকে যায়, তখন বাংলার মাটিতে এক বিশেষ স্পন্দন অনুভূত হয়। ঘরের উঠোনে সিজগাছ (ফনিমনসা) রোপণ করে, মাটি ও মায়ের অব্যক্ত স্পর্শে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় মনসাদেবীর উদ্দেশ্যে। সেই উঠোনেই জেগে ওঠে বিশ্বাস, জেগে ওঠে আতঙ্কের স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি—সর্পভীতি, যা যুগ যুগ ধরে মানুষের চেতনার গভীরে গেঁথে আছে। ঠিক তেমনি, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতেও বাংলার এক বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে মনসার বন্দনার ধ্বনি। এককালে যা ছিল একান্ত পারিবারিক আচার, আজ তা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে; গ্রামবাংলার একান্ত মন্দির থেকে শুরু করে বৃহত্তর জনসমাবেশেও পূজিতা হচ্ছেন দেবী।
মনসা যেন শুধু একটি দেবীমূর্তি নন, তিনি এক সামাজিক চেতনার প্রতীক, এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। বিশেষত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে মনসার উপস্থিতি আরও গভীর, আরও আন্তরিক। কৃষকের ঘরে ঘরে তাঁর বেদী, তাঁর ‘থান’ একান্তভাবে জড়িয়ে আছে জীবনের সঙ্গে—সেই জীবন, যেখানে ধানচাষের প্রতিটি কাদামাখা পা যেন তার পাশে এক অদৃশ্য আশীর্বাদ খোঁজে।
অখণ্ড দিনাজপুরের এক অংশ, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের ফুলঘড়া, সেখানে শরৎকালে দূর্গাপূজার পরিবর্তে মনসা পূজা হয়। ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে এ পূজা হচ্ছে। পুরনো এই পূজার ধারা যেন জানান দেয়, সংস্কৃতি কেবল ধর্মাচারের নয়, জীবনের ধারাবাহিকতাও।
উত্তরবঙ্গে মনসা অনেক ক্ষেত্রেই আত্মোপলব্ধির ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে মিলেমিশে ওঠে পারিবারিক আখ্যানে। দিনাজপুরের রাজবাড়ি এলাকায় ঘোষপাড়ার গোলকেশ ঘোষের অভিজ্ঞতা যেন এই পূজাকে আরও মানবিক, আরও বাস্তব করে তোলে। আজ থেকে সত্তুর বছর আগে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি—স্বপ্নে তাঁর বড় ছেলে কালীকেশ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছে, আর মনসা দেবী তাঁকে রক্ষা করতে বলছেন পূজার বিনিময়ে। সেই ভোরে জেগে উঠে দেখলেন ছেলে অক্ষত। সেই মুহূর্ত থেকে যেন বিশ্বাস এক নতুন জন্ম পেল তাঁর মনে, এবং মনসা পূজার যে রেওয়াজ তিনি শুরু করেছিলেন, তা আজও তাঁর বংশধরদের কাছে জীবন্ত। এই স্মৃতি শুধু পারিবারিক আবেগ নয়, তা এক জাতিগত সংস্কৃতির অংশ, যেখানে স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমানা অস্পষ্ট।
আমি এই অঞ্চলের নানা স্থানে নিজেও দেখেছি রাজবংশী বাড়ির পেছনের উঠোনে সিজগাছের পাশে প্রদীপ জ্বলছে, যেখানে ধ্বনিত হচ্ছে প্রার্থনা আর লোকগানের সুর। আমাদের সমাজে যেখানে চিকিৎসা ও বিজ্ঞান প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেখানেই সমান্তরালে বয়ে চলেছে বিশ্বাসের এক অন্তঃসলিলা, যা শুধু রোগ বা মৃত্যুভয়ের প্রতিকার নয়, বরং আত্মার আরাম। মনসা যেন একদিকে অতীতের সাপ-আক্রান্ত গ্রামজীবনের প্রতিচ্ছবি, আবার অন্যদিকে আধুনিক জীবনের উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা ও আত্মিক চাহিদার এক নিঃশব্দ জবাব।
এই পূজার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বও গভীর। এটি কেবল সর্পদংশনের প্রতিকার নয়, বরং এক বৈষয়িক জীবনের বিপরীতে আত্মিক পরিতৃপ্তির উৎস। যখন একজন কৃষক মনসার থান তৈরি করেন, তখন সেটি শুধু আধ্যাত্মিক ভরসা নয়, বরং এক সামাজিক পরিচয়ের চিহ্ন। এই পূজা আমাদের বলে, সংস্কৃতি শুধুই শহুরে নাট্যমঞ্চে হয় না—তার শেকড় অনেক গভীরে, মাটির কাছাকাছি, স্মৃতির ভিতর, আর বিশ্বাসের গভীরে।
চলমান সময়ে যখন আমরা প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করি—কীভাবে অতীতের ধর্মীয় আচার এখনো টিকে আছে, তখন মনসা পূজার মতো আচারগুলি আমাদের শেখায়, যে আচার তখনই টিকে থাকে, যখন তার পেছনে থাকে অভিজ্ঞতার সত্যতা, এবং তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় মানবজীবনের মৌলিক ভয়, আশা ও আরাধনার এক সজীব ভাষা। এই ভাষা কখনো মন্ত্রে, কখনো স্বপ্নে, আর কখনো পারিবারিক মিথের মধ্যে দিয়ে বর্তমানকেও সংলগ্ন করে ফেলে অতীতের সঙ্গে। এবং সেই সংলগ্নতার মধ্যেই, মনসা শুধুই এক দেবী নন—তিনি এক উত্তরাধিকার, এক চলমান চেতনা।
ড. মাসুদুল হক, কবি ও কথাশিল্পী